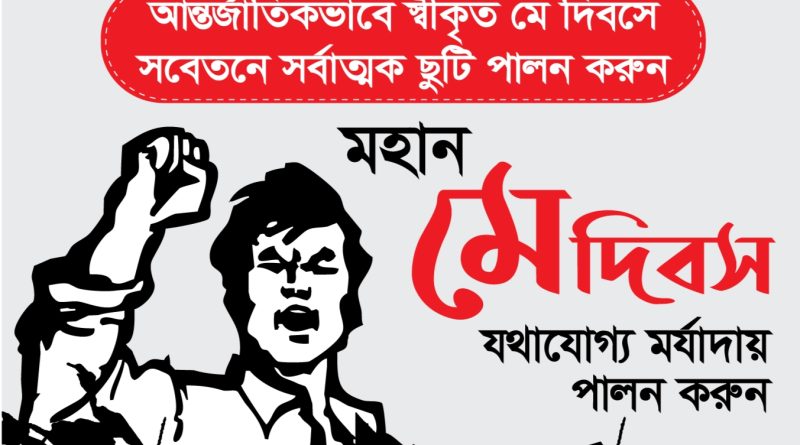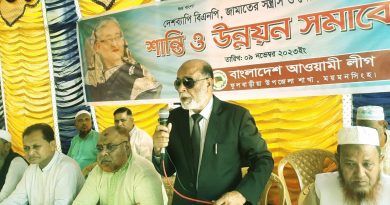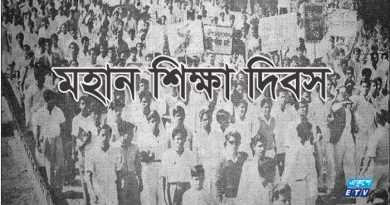মহান মে দিবসের বিপ্লবী চেতনা শ্রমিক শ্রেণীর কাছে চিরদিন অমলিন
তফাজ্জল হোসেন: বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণির কাছে মে দিবসটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। এই দিবসের তাৎপর্যের গভীরতা বোঝা যায় মহামতি এঙ্গেলস এঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, “ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমিক শ্রেণি একটি সৈন্য বাহিনী হিসেবে, একই পতাকা তলে একটি মাত্র লক্ষ্য পূরণের জন্য সংগ্রাম করেছেন- সেই লক্ষ্য হলো, আট ঘন্টা কাজের দিনকে আইনের স্বীকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা।” ৮ ঘন্টার কাজের দাবিতে এই আন্দোলন মালিক শ্রেণির বুকে কি রকম কম্পন তৈরি করেছিল তা বোঝা যায় সাপ্তাহিক ওয়ার্কার নামে একটি পত্রিকায় ১৯২৩ সালের মে দিবস সংখ্যায় একটি লেখার মাধ্যমে। চার্লস রুদেনবার্গ নামে একজন পত্রিকাটিতে লেখেন- “মে দিবস পুঁজিবাদীদের বুকে জাগায় আশংকা আর সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের বুকে জাগায় আশা”। কিন্তু বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা শ্রমিকদের এই মনোভাবকে ‘সামাজিক যুদ্ধ’ ও ‘পুঁজির প্রতি ঘৃণা’ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন।
আজকের সময়ে ৮ ঘন্টার শ্রমের দাবি বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই রাষ্ট্রীয় আইনস্বীকৃত। ফলে মালিকশ্রেণির প্রচার হচ্ছে মে দিবসের তাৎপর্য শেষ হয়ে গেছে। তাই মালিক শ্রেণির প্রতিপালিত শ্রমিক সংগঠন ও তার নেতাদের কাছে মে দিবস হচ্ছে বিশ্রাম ও চিত্ত বিনোদনের দিন। যেহেতু এই দিনে শ্রমিকের রক্ত ঝরিয়েছে সেহেতু তাদের কাছে এটি বড়জোর কিছু আনুষ্ঠানিকতার বিষয়। তাদের জবাবে মে দিবসের বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সামনে আনা জরুরি কর্তব্য। ৮ ঘন্টার শ্রম দিবসের দাবিতে মে দিবসের আন্দোলন সংগঠিত হলেও মে দিবসের আগে বা পরে শুধু ৮ ঘন্টা শ্রমদিবসের দাবিতেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে নি। মে দিবস বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক সংগ্রামের বিকাশের একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়। এই অধ্যায়টি রচিত হওয়ার প্লট তৈরি হয়েছিল তার ঐতিহাসিক পরিক্রমাতেই। আমেরিকা আবিস্কার ও আফ্রিকা প্রদক্ষিণের ফলে ইউরোপে উঠতি বুর্জোয়াদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে যায়। পূর্ব ভারত, চীনের বাজার, আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন, উপনিবেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিময়-ব্যবস্থার তথা সাধারণভাবে পণ্যের প্রসার- বাণিজ্যে, নৌযাত্রায় ও শিল্পে অভূতপূর্ব একটা উদ্যোগ তৈরি হয়। এর দ্বারা টলায়মান সামন্ত সমাজের অভ্যন্তরস্থ বৈপ্লবিক উপাদানগুলি দ্রুত পুঁজির বিকাশ ঘটায়।
পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ- এই তিন শতাব্দী ধরে বণিকতন্ত্রের যুগে ঔপনিবেশিক দেশগুলি থেকে লুটতরাজ ও ডাকাতির মাধ্যমে ইউরোপে আদি পুঁজির সঞ্চয়ন ঘটে। এ পুঁজি দিয়ে ইউরোপে তৈরি হতে থাকে মিল কলকারখানা। ক্ষয়িষ্ণু সামন্তীয় ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে শিল্প বিকাশের রাজনৈতিক অনূকূল পরিবেশ তৈরি করে বণিকরা। সামন্তীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষয়িষ্ণু ও নি:শেষ হওয়ার দরুণ গ্রামীণ গরীব, ভূমিহীন ও সর্বহারা মানুষেরা ভীড় করতে থাকে শহরের মিল কলকারখানাগুলিতে। কত টাকা মজুরিতে কত ঘন্টা কাজ করবে- তা নিয়ে দরকষাকষি করার সুযোগ নেই তখন। শ্রমিকের কর্মঘন্টা নির্ধারণ বা চাকুরির নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় কোন আইন তখন প্রণয়ন হয় নি। এ সময়ে পৃথিবীতে আবিস্কার হতে থাকে উৎপাদনের নতুন নতুন যন্ত্র। ফলে যন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করে নিজেদের রুটি রুজি টিকিয়ে রাখতে হিমসিম খেতে হয় শহরে নতুন আগন্তুক এই শ্রমিক শ্রেণিকে।
১৮ থেকে ২০ ঘন্টা এই শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক কাজ করতে হয়। এই অবস্থায় তাদের আয়ুস্কাল কত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তবে একটা যন্ত্রেরও তো নির্দিষ্ট জ্বালানী দরকার, যা না হলে যন্ত্রটি আর চলতে চায় না। তেমনি একজন শ্রমিকের জীবনী শক্তি রক্ষার জন্য তার প্রয়োজনীয় খাদ্য, ঘুম ও বিশ্রামের দরকার। তা না হলে সেও আর শ্রম দিতে সক্ষম থাকে না। পুঁজির মুনাফার জন্যও শ্রমিকের এই জীবনী শক্তি রক্ষা করা দরকার। কারণ শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে কারখানার উৎপাদনশীলতা। অথচ সেই শ্রমিকের সক্ষমতা বাড়াতেই মালিকগোষ্ঠীর যত উদাসীনতা আর অবহেলা। পুঁজিবাদের তখন রঙ্গিন সময়, পাগলা ঘোড়ার মতো সমগ্র ইউরোপব্যাপী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সামন্তীয় ব্যবস্থার স্থলে অধিষ্টিত নতুন ব্যবস্থাটি। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও তখন এই পাগলা ঘোড়াটিকে ছুটিয়ে নেয়ার দিকে, শ্রমিকের জীবনমানের দিকে ইউরোপের নতুন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর তখন পিছনে ফিরে তাকানোর জো নেই। শ্রমিক কত ঘন্টা কাজ করে কত টাকা মজুরি পাবে – তা নিয়ে রাষ্ট্রের আইন নেই ও মাথাব্যথাও নেই। এমন অবস্থাতেও শহরে প্রতিনিয়ত ভীড় করছে শ্রমিকের দল। পেটের তাগিদে কোন দরাদরি না করেই কারখানায় ঢুকে পড়লেও অল্প সময় পরেই তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় অমানুষিক খাটুনি আর বেহিসেবি কর্মঘন্টার প্রেক্ষিতে সোচ্চার হওয়া শুরু করলো। প্রথম প্রথম বিচ্ছিন্নভাবে শ্রমিকরা প্রতিবাদ করে দেখলো, তাদের উপর আরও বেশি দুর্ভোগ নেমে আসে। এরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক পর্যায়ে তারা আবিস্কার করলো- একসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করলে বা দাবি-দাওয়া জানালে তাদের দুর্ভোগ কম হয়। বরং মালিক ও কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে আলোচনা করে সমস্যা মেটানোর চেষ্ঠা করে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই শ্রমিকরা জন্ম দিলো গিল্ড বা সমিতি (পরবর্তীতে এগুলোই ট্রেড ইউনিয়ন নামে পরিচিত)।
ট্রেড ইউনিয়নের সুতিকাগার ইংল্যান্ডে হলেও বিশ্বের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকদের ইউনিয়নের জন্ম হয় ১৮২৭ সালে। ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠার ফলে ১৮২০ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত কাজের কর্মঘণ্টা কমাবার দাবিতে ধর্মঘটের পর ধর্মঘট সংঘটিত হয়। ১৮৫০ সাল থেকে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার ব্যাপারে ইউরোপব্যাপী ব্যাপক কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আর তখন থেকেই দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের নিয়ম চালু করার দাবি জোরদার হতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ১৮৬৬ সালের ২০ আগষ্ট ৬০ টি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি বালটিমোরে মিলিত হয়ে ‘ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন’ প্রতিষ্ঠা করে। শ্রমিকদের এই জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন ঢালাই শ্রমিকদের ইউনিয়নের নেতা উইলিয়ম এইচ. সিলভিস। বয়সে তরুণ এই শ্রমিক নেতা লন্ডনস্থ প্রথম আন্তর্জাতিকের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর মাধ্যমেই প্রথম আন্তর্জাতিকের সাথে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাকালীন সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়- “এই দেশের শ্রমিক শ্রেণিকে পুঁজিবাদীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য এই মূহুর্তে প্রথম ও প্রধান আয়োজন হলো এমন একটি আইন করা, যার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যেই সাধারণ কাজের দিন হবে আট ঘন্টা। এই মহান লক্ষ্য পূর্ণ করার পথে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করবার সংকল্প আমরা গ্রহণ করছি”। এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই প্রথম আন্তর্জাতিক এর জেনেভা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। লেবার ইউনিয়নের দাবির সমর্থনে কংগ্রেসে বিবৃতি দেয়া হয়। বিবৃতিতে বলা হয়- “কাজের দিন আইন করে সীমাবদ্ধ করে দেয়া একটা প্রাথমিক ব্যবস্থা; এই ব্যবস্থা ছাড়া শ্রমিক শ্রেণির উন্নতি ও মুক্তির পরবর্তী সব প্রচেষ্টাই নিস্ফল হতে বাধ্য। –কাজের দিন আট ঘন্টার আইন করে বেঁধে দেবার প্রস্তাব কংগ্রেস উত্থাপন করছে।’ কিন্তু আন্দোলন গড়ে তোলার পর্যায়েই সিলভিসের মৃত্যু হয় এবং এর পরে নেতৃত্ব সংকটের কারণে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের বিপর্যয় শুরু হয় এবং ক্রমে এর বিলুপ্ত ঘটে। পরবর্তীতে ‘‘আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার’ এবং ‘নাইটস অব লেবার’ ১লা মে শ্রমিক ধর্মঘটের কর্মসূচি অগ্রসর করে নিয়ে যায়। কিন্তু ধর্মঘটের সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো ‘নাইটস অব লেবারের’ নেতারা আন্দোলনকে স্যাবোটাজ (ভিতর থেকে আঘাত) করতে লাগলো। এমনকি গোপনে তাদের ইউনিয়নগুলিকেও ধর্মঘট না করার পরামর্শ দিতে লাগলো। তবে দেখা গেলো, এতে ফেডারেশনের মর্যাদা আরও বেড়ে গেলো এবং উভয় সংগঠনের সাধারণ কর্মিরাই উৎসাহের সঙ্গে ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিতে থাকলো। শহরে শহরে আট ঘন্টা শ্রম সমিতি গড়ে উঠল। সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনে একটা নবজাগরণ সৃষ্টি হলো। অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যেও এর ছোঁয়াচ লাগলো। যার ফলশ্রুতিতে জন্ম হলো রক্তাক্ত মে দিবসের।
শ্রমিক শ্রেণীর এই রক্তঝরা সংগ্রামের কারণে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া মে দিবসকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার সাহস পায় না। কিন্তু মে দিবসের বিপ্লবী তাৎপর্যকে ম্লান করার জন্য মালিকশ্রেণী ও তাদের তাবেদার সারা দুনিয়ার রাষ্ট্র ও সরকারসমূহ বিভিন্নভাবে প্রলেপ লাগিয়ে মে দিবসের সংগ্রামী তাৎপর্যকে আড়াল করতে চায়। বাংলাদেশ সরকার এ বছর মে দিবসের স্লোগান নির্ধারণ করেছে “শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলি”। সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে দিয়ে এই দিবসটি সরকার পালন করে। কিন্ত মালিক শ্রেণীর সাথে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য গড়ার নামে শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করার এই যে সরকারের হীন চেষ্ঠা তা কখনো হালে টিকবে না। কারণ শ্রম-পুঁজির দ্বন্দ্ব চিরন্তন। মালিকরা পুঁজির মানাফার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে তীব্র শোষণ করার ক্ষেত্রে কোন ছাড় দিবে না। তাই শ্রমিক শ্রেণীও তার মজুরি ও জীবনমান রক্ষার জন্য মালিক শ্রেণীকে ছাড় দিবে না। তবে শ্রমিক শ্রেণী যদি ঐক্যবদ্ধভাবে পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাহলে মালিকের মুনাফার সাথে সাথে ধনীক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সরকারগুলিও খাদের কিনারায় গিয়ে পড়বে। তাই এসব উচ্ছিষ্টভোগী সরকারগুলি সবসময় চায় রাষ্ট্রীয় আইন ও শক্তি দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে দমন-পীড়ন ও নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে। আবার কোন সময় কৌশলে শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনাকে বিভ্রান্ত করতে শ্রমিক দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্ঠা করে। সরকারের “মালিক-শ্রমিক ঐক্যের” স্লোগানের মাধ্যমেও কিছু সংখ্যক শ্রমিককে যুক্ত করে মে দিবসের তাৎপর্যকে খর্ব করার চেষ্ঠা করে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ৮ ঘন্টা কর্মদিবস নির্ধারণের বাহবা নেয়ার প্রচার দিলেও প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের কোন সেক্টরের শ্রমিকই ৮ ঘন্টায় কর্মদিবসে তার কর্ম শেষ হয় না। যেসব প্রতিষ্ঠানে আট ঘন্টার আইন কার্যকর করা হয়, সেখানে ওভারটাইম খেটে তার কর্মঘন্টা ১২/১৪ ঘন্টায় ঠেকে। এছাড়াও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে আট ঘন্টার কর্মদিবস কার্যকর না হওয়ায় ১৪/১৫ ঘন্টা এমনিতেই খাটতে হয়। শুধু তাই নয়, ১৪/১৫ ঘন্টা দৈনিক খেটেও শ্রমিক ও শ্রমজীবি মানুষেরা তাদের সংসার সামলাতে হিমসিম খায়। ফলে আরো ২/৪ ঘন্টা তার নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের বাইরে খেটে সংসারের অভাব দূর করার চেষ্টা করে। এভাবে দেখা যায় ১৩৯ বছর আগে ৮ ঘন্টা কাজ, ৮ ঘন্টা আমোদ-প্রমোদ, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম- এই আওয়াজে মে দিবসের যে প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল, বাংলাদেশসহ বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর কাছে সেই প্রেক্ষাপট আজও জীবন্ত। যতদিন পর্যন্ত শ্রমদাসত্বের বিদ্যমান ব্যবস্থাটার উচ্ছেদ করা না যাবে, ততদিন শ্রমিক শ্রেণীর কাছে মে দিবসের তাৎপর্য নতুন নতুন মাত্রা নিয়ে হাজির হবে। (লেখক: যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ)